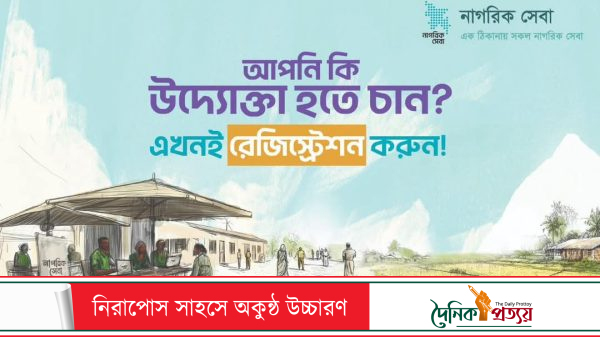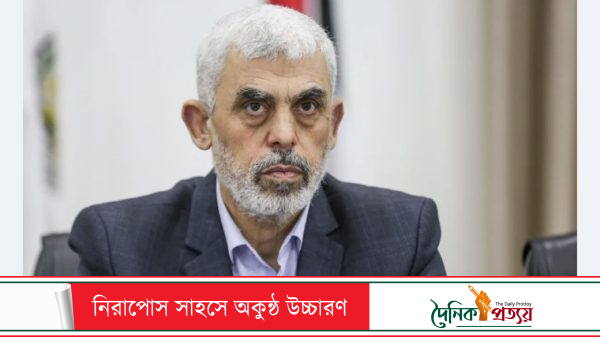ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি
- Update Time : সোমবার, ৮ জুন, ২০২০
- ২২৬ Time View

সায়েম আহমেদ
ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। প্রাক-ঐতিহাসিক কাল থেকে এ ভূমি উঁচু পর্বতমালা আর উত্তাল জলরাশি দিয়ে বিচ্ছিন্ন। এ অঞ্চল সব সময়েই আপন স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। প্রাকৃতিক সুরক্ষা, উর্বরা কৃষিভূমি, নদীভিত্তিক যোগাযোগ আর উদ্ভাবনী কুটির শিল্পের আশীর্বাদে এর জনগণ মোটাদাগে ছিল অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি। সাধারণ মানুষ খুব স্বাচ্ছন্দে না থাকলে খাওয়া পরার কষ্ট করেনি। ইউরোপীয় উপনিবেশে বাঁধা পড়ার আগে সে সময়ের মোট বৈশ্বিক জিডিপির এক চতুর্থাংশেরও বেশি উৎপন্ন করতো ভারতবর্ষ যার বড় অংশ আমাদের বঙ্গদেশ থেকে আসতো। এ ভারতবর্ষে কিভাবে উপনিবেশবাদের সূচনা হলো!
ইউরোপিয়ানরা ভারতবর্ষ বা “আল হিন্দ” এর কথা জানতে পারে আরবদের কাছ থেকে। উভয়ের যৌথ পবিত্র ভূমি জেরুজালেম নিয়ে শতবর্ষী ধর্মযুদ্ধ দু’পক্ষকে দীর্ঘ সংস্পর্শে নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমারা জেরুজালেম হারালেও আরবদের থেকে বিজ্ঞান আর দর্শনের অভূতপূর্ব জ্ঞান লাভ করে। আর জানতে পারে “হিন্দ” এর অতুল সম্পদ আর লাভজনক মসলা বাণিজ্যের কথা। সম্ভাবনার হাতছানি তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়, যেভাবেই হোক ভারতবর্ষে যেতে হবে। কিন্তু, মাঝখানে যে শত্রু আরবভূমি। স্থলপথ না হোক অচেনা সাগর দিয়ে তো চেষ্টা করে দেখা যায়!
সমুদ্রাভিযানের অগ্রসৈনিক পর্তুগীজরদের মনোবল বাড়াতে পোপ নিকোলাস লিখিত বিবৃতি দেন, ভারতবর্ষ পর্যন্ত যেতে তারা যা আবিষ্কার করবে সে জল আর স্থলের উপর পর্তুগালরাজ হেনরির এককাধিকার থাকবে। মজার বিষয় হলো, এ ধর্মগুরু মনে করতেন ভারতবর্ষের অধিবাসীরা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী। তার অনুসারীরা ভারতভূমির সম্পদ আর ধর্মের টানে উল্টোদিকে গিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার (১৪৯২ সাল) করলেও মূল উদ্দ্যেশ্য অধরা রয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে, দীর্ঘ দশ মাস বার দিনের সমুদ্রযাত্রায় পর্তুগীজ নাবিক ও জলদস্যু ভাস্কো-দ্য-গামা’র কামানসজ্জিত জাহাজ ১৪৯৮ সালের ২০ মে ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে পৌঁছলো। এ আগমন ভারতবর্ষে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের সূচনামাত্র।
কালিকট তখন সারা দুনিয়ার মশলা বাণিজ্যের রাজধানী। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া আর ভারতবর্ষে উৎপন্ন গোলমরিচ, এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি আর অন্যান্য সুগন্ধি মশলা কালিকট বন্দর হয়ে পশ্চিমে সুদূর ভেনিস পর্যন্ত চালান হয়। বন্দরের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক। শত শত বছর ধরে ভারতীয়, আরবী, পারসিক, মিশরীয় আর গ্রীকরা বাণিজ্য করছে। ভাস্কো-দ্য-গামা এসেই পর্তুগীজদের জন্যে বন্দর শুল্কের অব্যাহতি চাইলেন। পাশ্ববর্তী একটি মন্দিরকে গীর্জা মনে করে প্রথমে পুলকিত হলেও ভুল ভাঙ্গতে সময় লাগলো না। কালিকটে আরব বনিকদের দেখতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। লক্ষ করলেন, এ জাত শত্রুরা তো শুধু বাণিজ্যই করছে না, কালিকটরাজ জামোরিনের সাথে তাদের রয়েছে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক। দেশে ফেরৎ গিয়ে তিনি তৎকালীন পর্তুগালরাজ ও পোপ স্বীকৃত পরবর্তী সমুদ্রাধিপতি ম্যানুয়েলকে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন।
এরপর বেশি সময় লাগলো না, পর্তুগীজদের তেত্রিশটি রণতরী আর অস্ত্রসজ্জিত পনেরশো যোদ্ধা বাণিজ্য করতে কালিকটে আসলো। রাজা জামোরিন তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ব্যবসা করার স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন। কিন্তু, তারাতো স্বাভাবিক ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবসার জন্যে আসেনি। আগুনের গোলায় স্বার্থসিদ্ধির পবিত্র দায়িত্ব পালনে এসেছে। তারা নির্বিচারে জলদস্যুতা, হত্যা আর অত্যাচার করতে লাগলো যা এ অঞ্চলের জন্যে এক নতুন অভিজ্ঞতা। শত শত বছরের শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের সিলসিলা চুরমার হয়ে যেতে লাগলো। পর্তুগীজদের অগ্নিবর্ষী কামান, চতুরতা আর ষড়যন্ত্র কিছুকালের মধ্যেই তাদের কালিকট থেকে সুদুর মালাক্কা ও জাভা পর্যন্ত লাভজনক মশলা ব্যবসার একক নিয়ন্ত্রণ এনে দিল। এ সাফল্য দেখে ইউরোপের অন্যান্য নৌশক্তির আফসোস ছাড়া কিছুই করার ছিল না। দৈববাণীযে পর্তুগালের পক্ষে।
এরমাঝে, মার্টিন লুথার খ্রিষ্টধর্মে প্রোটেস্টান্টবাদের এক নতুন ধারা নিয়ে এলেন। এখন আর পোপ সারা খ্রিস্টানজাহানের একাধিপতি নন। প্রথম ধাক্কাতেই ওলন্দাজরা ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে পর্তুগিজদের বাণিজ্য ছিনিয়ে নিতে লাগলো। এরপর,ফরাসিরাও আসলো একই উদ্দেশ্যে। এদের মধ্যে সবচেয়ে চতুর ইংরেজরা আসলো সবশেষে। এরা গৌরব আর শক্তিতেও অন্যদের চেয়ে বলীয়ান। বর্ণ-স্বজাতিদের বাণিজ্য আর লুটপাটের চেয়েও অনেক বৃহৎ সম্ভাবনা তারা খুঁজে পেল। অন্যদের হটিয়ে দিয়ে বণিকের মানদণ্ডের আড়ালে রাজদণ্ড দখলের প্রক্রিয়া সুচারুভাবে গুছিয়ে আনল। ভারবর্ষের শাসকবর্গের অদক্ষতা, আমাত্যদের সীমাহীন লোভ আর সামাজিক বিভেদের কারণে তাদের খুব বেগ পেতে হয়নি।
বুদ্ধিমান ইংরেজরা ভারতবর্ষের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় জায়গা বঙ্গদেশ খুঁজে পেতে ভুল করেনি। ঢাকা বা মুর্শিদাবাদের মতো শতবর্ষী নগর রেখে এক নব্যকৃত গ্রামে তাদের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র কলকাতা পত্তন করলো। ব্যবসা বাণিজ্যের আড়ালে সমরসজ্জা আর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে লাগলো। বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাবকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হারিয়ে (১৭৫৭ সাল) ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সূচনা করলো। এ করিতকর্মা জাতি ভাগ্যবিধাতা হতে এসেছে শুধু মসলার বাণিজ্য করতে আসেনি। পরবর্তী দুই শতাব্দীর “বিভাজন ও শাসন” আর পুঁজির পাচার ভারতবর্ষকে এক চতুর্থাংশ বৈশ্বিক জিডিপির গর্বিত অংশীদার থেকে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনে। ধর্ম ও আঞ্চলিকতার যে বিভক্তির সূচনা হয় তা আজও বহমান।
লেখক: